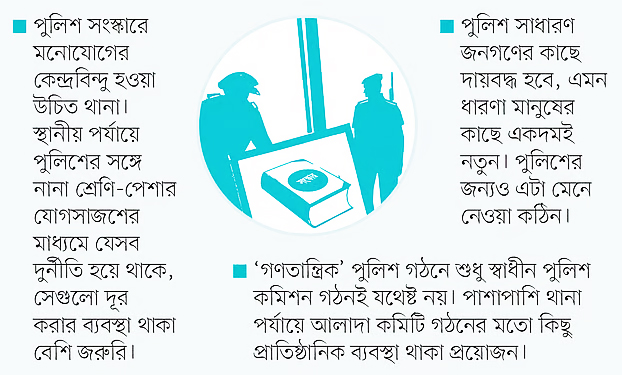পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে আবারও আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আলোচনার মূল বিষয় হলো, পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, পেশাদারিত্বের সাথে পরিচালনা করার জন্য একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন প্রতিষ্ঠা। এই কমিশনের ধারণা ছিল পুলিশ বাহিনীকে কার্যকরভাবে পরিচালনা করা, যাতে তারা ন্যায়বিচারের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে এবং জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে। পুলিশ কমিশন গঠনের জন্য রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত ও পেশাদারী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিশেষজ্ঞদের মধ্যে একটি সাধারণ মতামত ছিল। তবে বর্তমান পুলিশ সংস্কার কমিশন এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রস্তাব করেনি, বরং পরীক্ষার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু কেন কমিশন নিজেই পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রদান করেনি, সেটা এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের সদস্যরা তো বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন!
বর্তমান পুলিশি ব্যবস্থার ত্রুটি ও জনগণের প্রত্যাশা
বর্তমান পুলিশ বাহিনী রাজনৈতিক প্রভাবের অধীনে পরিচালিত হয়, ফলে তারা জনগণের সেবা নিশ্চিত করতে পারে না। জনগণকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একটি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, আইনের প্রতি অনুগত, এবং দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ। সংস্কারের জন্য পুলিশ কমিশন গঠন এমন একটি বিষয় যা বহুদিন ধরেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে, তবে এখন পর্যন্ত এর বাস্তবায়ন হয়নি।
পুলিশ বাহিনীর মূল কাজ হচ্ছে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। যাকে আমরা ‘রেজিম পুলিশ’ বলে থাকি। কিন্তু গণতান্ত্রিক পুলিশ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে জনগণের প্রতি পুলিশের দায়িত্ব পালন আরও কার্যকর ও ন্যায়সঙ্গত হবে। তবে শুধুমাত্র একটি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনই যথেষ্ট নয়, পুলিশি ব্যবস্থায় আরও কিছু প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপও প্রয়োজন, বিশেষত থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন।
পুলিশ সংস্কারের পুরোনো উদ্যোগ
২০০৫ সালে একবার পুলিশ সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এরপর ২০০৮-১০ সালের কৌশলগত পরিকল্পনায় পুলিশ বাহিনীর মিশন, দৃষ্টিভঙ্গি ও অগ্রাধিকার তুলে ধরা হয়েছিল। এসব পরিকল্পনার আওতায় পুলিশ বাহিনীর সাংগঠনিক সংস্কার, স্থানীয় জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বৃদ্ধি, নারী পুলিশ নিয়োগ এবং কম্পিউটারভিত্তিক ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তখনকার সময়ে উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের কাছে এসব পরিকল্পনা গুরুত্ব পায়নি, বরং তারা আমলাতন্ত্রের বাইরে পুলিশ বাহিনীকে আরও স্বায়ত্তশাসিত করতে চাইছিলেন, যাতে রাজনৈতিক প্রভাব বজায় থাকে।
এছাড়া, ২০০৫ সালের সংস্কারের মাধ্যমে কিছু পদক্ষেপ যেমন মডেল থানা, ওপেন হাউস ডে, এবং কমিউনিটি পুলিশিং ফোরাম চালু হয়েছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ক্যাডারদের বিরোধিতার কারণে এ সংস্কারের কাঠামোগত পরিবর্তন সম্ভব হয়নি।
থানা স্তরের পুলিশ সংস্কার
পুলিশ সংস্কারে সবচেয়ে বড় গুরুত্ব দেওয়া উচিত থানা পর্যায়ের পুলিশি ব্যবস্থাকে। থানা স্তরের পুলিশিংয়ে যে সব দুর্নীতি ঘটে, সেগুলো দূর করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক উন্নয়ন করা। এর মাধ্যমে পুলিশ বাহিনী একটি সহযোগিতামূলক শক্তি হিসেবে কাজ করবে, যেখানে তারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারবে এবং আইন প্রয়োগে আরও ন্যায়বদ্ধ হবে।
গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা
বর্তমানে পুলিশকে কর্তৃত্বপরায়ণ সংস্থা হিসেবে দেখা হলেও, তাদের ভূমিকা যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তা সবাই মানে। পুলিশ বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মতে, পুলিশকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ করে গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা দরকার। এ ধরনের ব্যবস্থায় পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে, ফলে পুলিশ বাহিনী আইন প্রয়োগে আরও কার্যকর হবে এবং সরকার পরিবর্তনের পরও তাদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকবে।
নতুন পুলিশের কাঠামো: কমিটি ও জনগণের অংশগ্রহণ
গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত করার জন্য থানা পর্যায়ে কমিটি গঠন করতে হবে। এসব কমিটি স্থানীয় জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং তাদের মাধ্যমে পুলিশকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হবে। কমিটিগুলো হবে এমনভাবে গঠিত, যাতে এটি পুলিশের স্বেচ্ছাচারিতা ঠেকাতে সক্ষম হয় এবং পুলিশের সাথে জনগণের সম্পর্ক আরও ভালো হয়।
কমিটি গঠন করতে হবে প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে, যারা থানার কার্যক্রম তদারকি করবেন। থানার ওসি হবে এই কমিটির সদস্যসচিব এবং কমিটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক হবে। জেলা পর্যায়েও অনুরূপ একটি কমিটি থাকবে, যেটি থানাগুলোর তদারকি করবে।
কমিটির কার্যকারিতা ও চ্যালেঞ্জ
এই কমিটি কার্যকরভাবে কাজ করতে হলে তাকে আইনি ভিত্তি এবং প্রশাসনিক স্বীকৃতি থাকতে হবে। আরও প্রয়োজন সামাজিক স্বীকৃতি এবং কমিটির সিদ্ধান্ত প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা। যদিও এই কমিটির মাধ্যমে পুলিশের উপর জনগণের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, তবে এ পদ্ধতিকে সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণ করতে কিছু সময় লাগবে।
এই ব্যবস্থা শুরুতে নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে পারে, তবে এটি বাস্তবায়িত হলে ধীরে ধীরে এর সুফল আসবে এবং পুলিশের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া দৃঢ় হবে।
উপসংহার
গণতান্ত্রিক পুলিশি ব্যবস্থার রূপরেখা কেবল একটি কমিশন গঠন বা কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এতে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে পুলিশ জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে। এটি এমন একটি ব্যবস্থার ধারণা, যেখানে পুলিশ ও জনগণ একসঙ্গে কাজ করবে এবং একে অপরকে রক্ষা করবে।